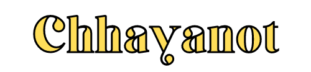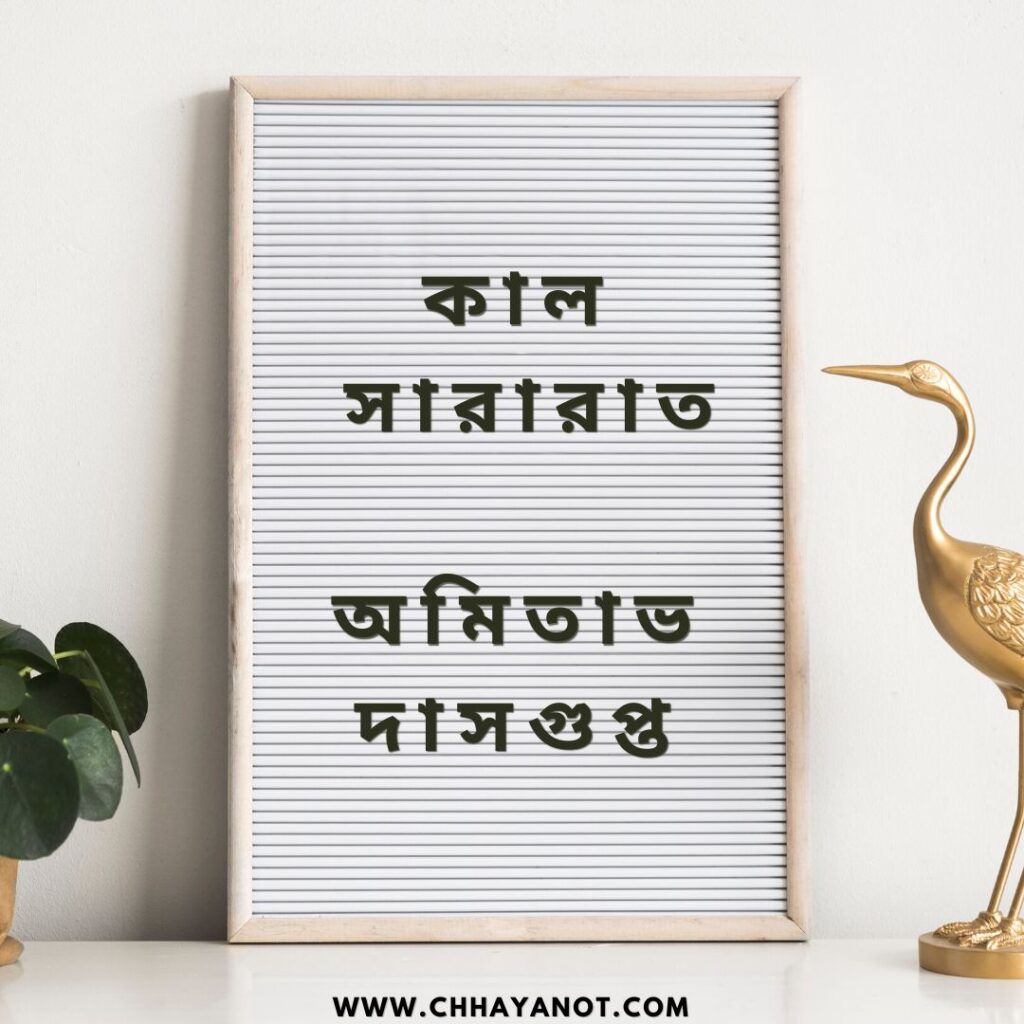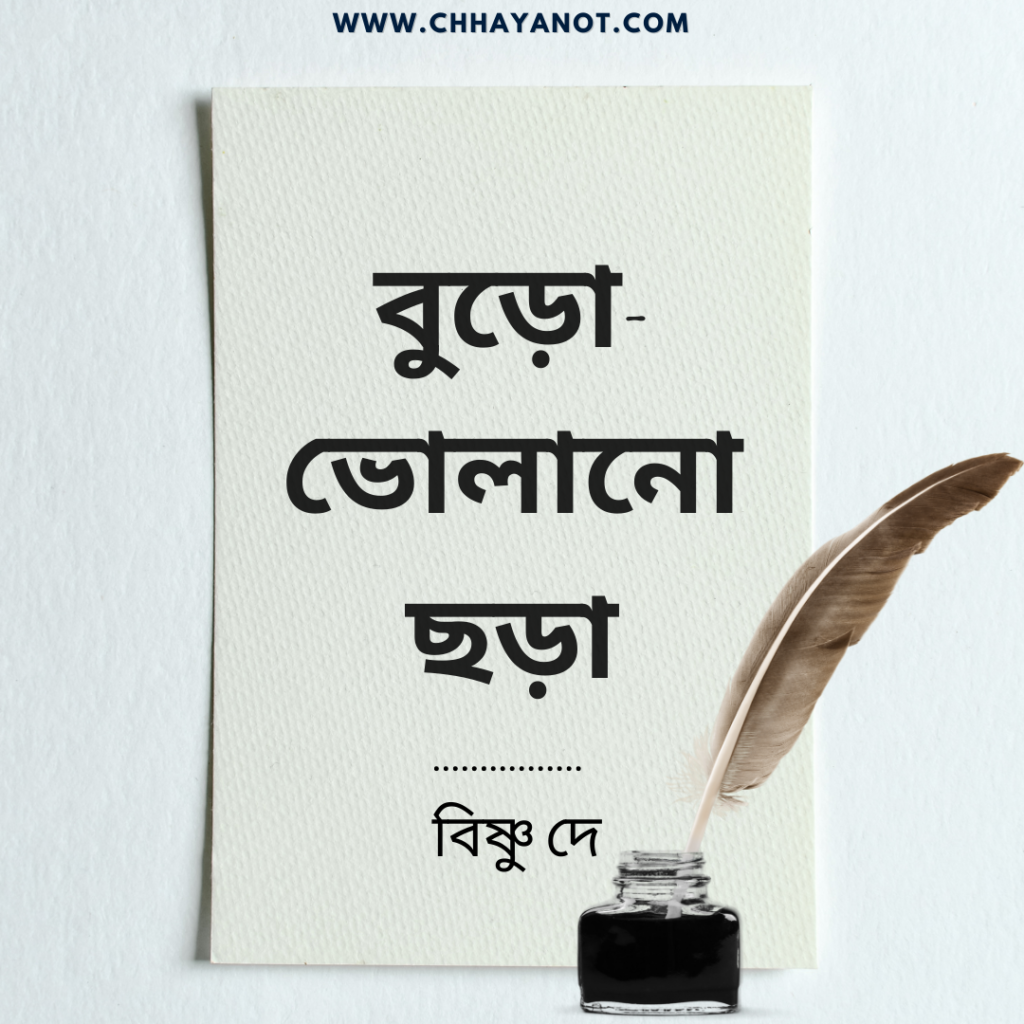রবীন্দ্রনাথ আমার খুব কাছের মানুষ নন
আবার খুব দূরবর্তী দারুমূর্তিও নন–
বয়সের হিসেবে তিনি আমার থেকে ঠিক নব্বই-বছরের বড়ো।
কিন্তু যদি আমাকে একটি দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়
শুধুমাত্র দশটি বই বেছে নেওয়ার অধিকার দিয়ে—
আমি অন্তত চার-পাঁচটি বই নেব রবীন্দ্রনাথের,
গল্পগুচ্ছ,তিনসঙ্গী তো নেবই
সঙ্গে থাকবে শেষের কবিতা ,গীতবিতান।
আর একটি বা দুটি কবিতার বই।
যদি এগারো বা বারো বইটি তুলে নিতে বলা হয় শেষমুহূ্র্তে
তাহলে অবশ্যই নেব বিসর্জন বা ডাকঘর,
শ্যামা বা রাজা ,রবিজীবনী বা উপকাব্য রবীন্দ্রনাথ।
ভয় হয় রবীন্দ্ররচনাবলী শেষে
আমাদের সেই ধর্মগ্রন্থে পরিনত না হয় ।
যার কাছ থেকে বার বার অজ্ঞাত ভয়ে
পালিয়ে গিয়েও ফিরে আসতে হয়
অজ্ঞাত এক আকর্ষণে।।
(ঝড় ঝড় ঝড় ঝড় ঝড়ের রঙের ঝড়না ,আয়…(গান)
পাঁচই মার্চ ১৯৮৮—-
তখন বসন্ত উৎসবের হাওয়া লেগেছিল
পূর্বপল্লীর রুদ্রপলাসের —
আমরা হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পড়লাম
শেষে উত্তরায়ণে।
অন্যান্য বারের মতই
আবার সেই ধন্ধে পড়লাম
এই খিলান ,এই প্রকৃতি
এই সংস্কৃতি, এই নগরী
তৈরি করেছেন একজন কবি!
কবি তো নির্জনচারী ,
অথবা উত্তাল মাতাল,
হাঁটু গেড়ে বসা প্রেমিক অথবা—
দর্পিত সম্রাট ,প্রকৃতি মুগ্ধ অথবা —
নগড়বিদ্বেষী,
কিন্তু এর কোনটাই নন রবীন্দ্রনাথ।
এত প্রথাবিরুদ্ধ ব্যক্তিত্বের মানুষটিও
ক্রমে ধর্মভীরু বাঙালির কাছে হয়ে উঠেছেন রবিঠাকুর–
এটাই মজা ,আর এই ঠাকুরবাড়ী দর্শনের জন্য
যেমন একদিকে বার বার ছুটে যান
শহরের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবিরা,
তেমন গ্রামগঞ্জ ঝেঁটিয়ে লাক্সারি বাসে করে চলে আসেন
সহজপাঠ না পড়া ঠাকুর-দর্শনার্থীরা—-
তেমনই একদল,আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন
রবীন্দ্রনাথ ও ইন্দিরাদেবীর একটি ছবি।
ওই অবোধ ভীড় থেকে ছুটে এল মন্তব্য–
দ্যাখ দ্যাখ ,ইন্দিরাগান্ধী আর রবিঠাকুর’।
আমার পাশ থেকে পম্পা তখন থাকতে না পেরে
বলেই ফেলল–‘দেখুন,উনি ইন্দিরাগান্ধী নন্-
রবীন্দ্র্রনাথের ভাইঝি ইন্দিরাদেবী।
কিন্তু মন্তব্যকারীরা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর–
হেঁসে পম্পাকে উড়িয়ে দিয়ে বলল,
‘কিচ্ছু জানেনা রে,’
ইন্দিরাগান্ধী তো এখানে পড়তেন-
এটাই ওঁর ফটো।’
রবীন্দ্রনাথ যখন এতটাই জনসাধরনের
তখন বলতেই পারি-
বাঙালির বেসিক নিড্ পাঁচটি নয়-ছটি,
খাদ্য,বস্ত্র,বাসস্থান,প্রাথমিক শিক্ষা ও চিকিৎসা
এবং রবীন্দ্রনাথ।
তারপর ঠাকুরপুজো কে কি ভাবে করবে
তা তারাই ঠিক করে নেবে।
চায়ের দোকানের কেষ্ট হয়ত
সাঁইবাবা আর নেতাজীর ফটোর মাঝখানে টাঙানো
রবীন্দ্রনাথের ফটোয় ধূপ জ্বালিয়ে সন্ধ্যে দেয়।
আর রবীন্দ্র গবেষিকা নীল আঁচল উড়িয়ে
রতনকুঠি থেকে চলে যান রবীন্দ্রভবনের দিকে।
মনে করা মুশকিল আমি কবে প্রথম রবীন্দ্রনাথের
কোন গানটি শুনেছিলাম।
তবে আমাদের বাড়িতে একটি পাগলা ভিক্ষুক আসত–
সে গাইত,’ওই মালতি লতা দোলে ‘,
সে প্রত্যেকটি শব্দের শেষে ‘ম’ অক্ষরটি যোগ করে দিত,
অর্থাৎ সে গাইত ‘ওইম মালতি লতাম দোলেম”,
কিন্তু তার কন্ঠটি ছিল বড় মায়াময়
কোনদিন ভুলব না–
আমি কখনও গান শিখিনি
মা বলতেন,’গলায় সুর নেই ,’
আমার আশপাশ দিয়ে সমবয়সীরা
গানের খাতা নিয়ে চলে যেত বিকেলের ক্লাসে ,
ওই রাজ্যটি ছিল আমার চেতনার বাইরে ।
কিন্তু জন্মাবধি কতবার কতভাবে যে
রবীন্দ্রগান গাইতে শুনেছি মানুষকে–
যখন ট্রেনে করে ইউনির্ভাসিটি যেতাম
এক কুষ্ঠ রোগী গাইত —
‘দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না’।
বলাবাহুল্য সে না জেনেই গাইত।
মাত্র ছাব্বিস বছর বয়সে বিধবা হওয়া
আমার এক পরিচিত মেয়ের গলায় শুনেছিলাম-
‘আমার দিন ফুরালো,ব্যাকুল বাদল সাঁঝে,’
একটি রূপহীন মেয়ে বিয়ে না হওয়া
যন্রনায় যে ক্রমশ মূক হয়ে আসছিল
সমবেত পাত্রপক্ষকে শুনিয়েছিল
‘বাঁচাও তাহারে মারিয়া’।
এমনিতে যে গান অসংখ্যবার শুনেছি
এক বিশেষ পুরুষের গলায় সেই গান শুনে
আমুল কেঁপে উঠেছিলাম —
তারপর থেকে বদলে গিয়েছিল
আমার জীবনের গতিপথ।
লোকালয়ে যেভাবে ধীরে ধীরে বন্যার জল ঢোকে —
এবং যেভাবে জনপদ তলিয়ে যায় জলের তলায়
সেইভাবে ধীরে নিশ্চিতভাবে আমরা কখন ডুবে গেছি —
গীতবিতানের অসামান্য লিরিকগুলোর তলায় ।
এমন স্রষ্টাকে প্রনাম না জানিয়ে পারিনা ।
তার সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।
এইসব সময়ে আমরাও তাকে অলৌকিক বলে ,
ঠাকুর বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।
তাকে অর্ধেক বুঝে ,অর্ধেক না বুঝে ,
মনে হয় তিনি এক অতিকায় একটা ডাকট্রিল
যার প্রাগৈতিহাসিক ডানার নিচে
নিশ্চিন্তে ঘরকন্যা করছে আমাদের আবহমান সংস্কৃতি।
বেলা,অবেলা ও কালবেলার মাঝখানে
অনড় দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ
–আমার রবীন্দ্রনাথ–তাঁকে প্রনাম।।